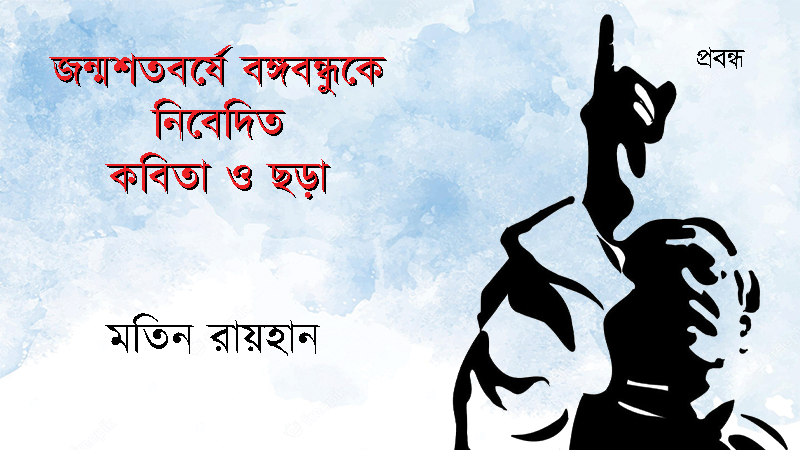আমার প্রায় নব্বই ছুঁই ছুঁই দিদি শাশুড়ি মানে বড়মার পনের বছরের পুরনো আয়া প্রতিমা দিদির হঠাৎ সখ হলো সে তীর্থ করতে যাবে। এতদিন বড়মার সব কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে তার উপোস, বারব্রত, গলায় কণ্ঠি ধারণ, অলস শান্তির দুপুরে ফুল ভলিউমে ইউটিউবে কীর্তন শোনা কিছুই বাদ ছিল না। সুখের বিষয় বড়মা কানে কম শোনেন আর আমরা দুপুরে প্রায় কেউই বাড়ি থাকি না। এত সব কিছুর পরেও তার তীর্থ করার সাধ হলো! আসলে পথের নেশা বড় নেশা। বড়মা তার এক নম্বর উদাহরণ। নিজে একসময় ভ‚গোলের অধ্যাপিকা ছিলেন। মেয়েদের নিয়ে সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরেছেন, তারপর অবসর নেওয়ার পর থেকে শুরু হয়েছে তাঁর পৃথিবী ভ্রমণ। আমি যদিও সে সব চোখে দেখি নি, গত দশ বছর বড়মা বাড়ি থেকে বের হন নি বললেই হয়, শুধু বছরে নিয়ম করে দিন সাতেকের জন্য হাসপাতালে থেকে আসা ছাড়া। তবে ছবি দেখেছি, গল্প শুনেছি, ওঁর বেড়ানো নিয়ে লেখাও পড়েছি। বড়মা আমাদের আবাসনের শারদ পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন কিনা। আর প্রতিমা দিদি আসার পরে কাছাকাছি কোথাও গেলেই তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এই করে করে তারও পুরী, কাশী, বৃন্দাবন ঘোরা হয়ে গেছে। তো এর সবই তো তীর্থ ভ্রমণ, নাকি! না তাতে হবে না। এগুলো ঘুরতে তো তাকে যথেষ্ট কষ্ট করতে হয় নি, প্রাণপাতও করতে হয় নি। অনাহারে, নিঃসম্বল হয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে অভীষ্ঠে পৌঁছতে হয় নি। ওসব না করলে নাকি সত্যিকারের তীর্থ দর্শন হয় না!
তা হতেই পারে। কথাটা শুনে হাসি পেলেও পরে ভেবে দেখলাম ধারণাটা নেহাৎ ভুলও নয়। আসলে তীর্থ দর্শনের মধ্যে বোধহয় কোথাও একটা কৃচ্ছ সাধনের অনুষঙ্গ থাকে। সেই যে দীর্ঘ অদর্শনের পর দয়িতকে দেখলে যেমন আনন্দ হয় অনেকটা সেই রকম।
আচ্ছা, ব্রতের ক্ষেত্রেও কি তাই নয়! ভবিষ্যতে কোনো একটা কিছু পাওয়ার জন্য, অর্থাৎ এই মুহূর্তে যেটা পাচ্ছি না তাকে চেয়ে বা কামনা করেই তো ব্রতগুলো পালন করা হয়। অর্থাৎ একটা অতৃপ্তি, আর তার থেকেই ব্রত পালন। মধ্যে যে শূন্যতাটা সেটা ভরে উঠছে নানান কল্পনায়, সেটাই হলো ব্রত আচরণ, যার মধ্যে আমরা নিজেকে জড়িয়ে দিচ্ছি, আলপনা আঁকছি, ব্রতের গান রচনা করছি, ছড়া বাঁধছি, তারপর সেই সবকিছু দিয়ে ব্রত পালন করছি, আর সব শেষে অনেক প্রতীক্ষার পর সত্যি যখন সেই কামনা চরিতার্থ হয় তখনকার যে আনন্দ সেতো বলার মতো নয় – চট করে চাইলাম আর ঝট করে পেয়ে গেলাম তাতে তো এই আনন্দটা নেই, একেবারেই নেই। তাতে যেন কামনার বিষয়টিও ভারি সাধারণ হয়ে যায়, সে যতই অমূল্য হোক না কেন। খানিকটা যেন ওই তীর্থ যাত্রার মতোই। লক্ষ্য করুন ওই ‘যাত্রা’ কথাটা। এই কথাটার মধ্যে একটা দীর্ঘ বহমানতা আছে। যেটা অনেক দিন ধরে চলছে, অনেক সময় ধরে, ধারাবাহিকভাবে। যেই মুহূর্তে আমি সেই যাত্রা শুরু করলাম অমনি আমিও সেই ধারাবাহিকতার অংশ হয়ে গেলাম। এ যেন বড় একটা সৌভাগ্যের মতো!
আমার এক ভাই আছে যার সাধ ছিল মার্কো পোলো যে পথ ধরে যাত্রা করেছিলেন সেই পথে সেও ভ্রমণ করবে। বোধহয় ড্যালরিম্পলের বই পড়ে তার ওইরকম ইচ্ছে জেগেছিল। ঠিক জানি না। তবে শেষ পর্যন্ত সে সিল্ক রুট ধরে একটা দিন কুড়ির সফর করেছিল। তা এও তো একধরনের তীর্থ ভ্রমণ। এতে তো সঙ্গতি থাকলেও পাঁচতারা হোটেল থাকছে না, শীতে গরমে অল্পবিস্তর কষ্ট করতে হচ্ছে, স্থানীয় যানবাহন, বস্তা, ঝুড়ি, ছাগল, কম্বল, বাচ্চাকাচ্চা, জলের কুঁজো, বাসন-কোসন সঙ্গে নিয়ে চলা মানুষদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে পথ চলতে হচ্ছে। এতে যে সহ্য ক্ষমতা বাড়ছে, সবার সঙ্গে মিলেমিশে চলতে গিয়ে যে বিনয় শিক্ষা হচ্ছে – মনে হয় এমন আর কিছুতে হয় না। এও তীর্থ ভ্রমণের এক অনন্য লাভ। যে মানুষটা দীর্ঘ পথে রওনা দিয়েছিল যাত্রা শেষে ঠিক সেই মানুষটাই আর ফিরে আসছে না কিন্তু। কাজেই প্রতিমা দিদিকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। সে অতশত না ভাবলেও কষ্ট করার কথাটা যে বলেছে সেটাই হলো তীর্থ ভ্রমণের মূল কথা। কাজেই ‘যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে’ – এই কথা এই মুহূর্তে অন্তত তাকে বলে কোনো লাভ নেই।
এ বছরের বইমেলা থেকে পাওয়া বন্ধুর উপহার স্বামী রামানন্দ ভারতীর ‘হিমারণ্য’ পড়ছিলাম। সেখানেও সেই একই ব্যাপার। দীর্ঘ বিপদ সঙ্কুল পথে প্রতি মুহূর্তে শারীরিক অসুস্থতাকে তুচ্ছ করে কৈলাস ও মানস সরোবরের পথে যাত্রা শুরু করেছিলেন পরিব্রাজক রামানন্দ স্বামী। একশ’ বছরের ও বেশি পুরনো এক সাময়িক পত্রিকায় লেখা সেই ভ্রমণ কাহিনী পড়ার তীব্র ইচ্ছে ছিল যেদিন লীলা মজুমদারের আত্মস্মৃতি ‘পাকদণ্ডী’ পড়েছিলাম সেইদিন থেকে। বস্তুত ওই বইতেই প্রথম এই লেখাটির কথা জানতে পারি। কারণ ঘটনাচক্রে এই রামানন্দ স্বামী ছিলেন লেখিকার দাদামশাই! প্রথম জীবনের রামকুমার বিদ্যারতœ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়ে আবার পরবর্তীকালে স্বধর্মে ফিরে আসেন, সন্ন্যাস নেন এবং স্বামী রামানন্দ ভারতী নামে পরিচিত হন।
রামানন্দ ছিলেন চিরপথিক। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত শরীর নিয়েও দুর্গম থেকে দুর্গমতর হিমালয়ের পথ পরিক্রমা করেছেন তিনি, আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে গেছেন একটি অমূল্য সম্পদ, তাঁর ‘হিমারণ্য’।
এই গ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, ‘প্রায় চারি বৎসর অতীত হইল, আমি মানস সরোবর ও কৈলাস প্রভৃতি তিব্বত দেশীয় তীর্থ ভ্রমণ করিতে হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বত দেশে যাত্রা করি। তিব্বতে যাইবার সময় তিব্বত দেশীয় কোন বিবরণ সংগ্রহ করিবার আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। … কিন্তু তথাকার নানা প্রকার রীতিনীতি দর্শন করিয়া এবং থুলিং মঠের বৃহৎ পুস্তকাগার ও দেবালয় সমূহ দর্শন করিয়া মনে হইল যদি আমি ইহা গোপন করিয়া যাই তাহা হইলে চিরদিন মুনি ঋষিদের নিকট ঋণী রহিব। এই মনে করিয়া তিব্বত ভ্রমণ লিখিতে আরম্ভ করি।’
তাঁর বর্ণনা অনাড়ম্বর। বাহুল্যবর্জিত এবং মেদহীন। একদিনের কথা লিখছেন, ‘অদ্যকার পথ বড় সুন্দর। অবরোহণ নাই। পর্বত শ্যামল তৃণে সমাবৃত; মাঝে মাঝে কণ্টক বৃক্ষ। অনেকদিন বরফ ভিন্ন শ্যামল তৃণ পর্যন্ত দেখিতে পাই নাই, অদ্য তাহা দেখিয়া বড় আনন্দ হইল।’
কেমন সহজ সুন্দর আনন্দ তাঁর প্রতিটি শব্দ ব্যবহারে।
আবার কৈলাস দর্শন করে লিখছেন, ‘হিমালয় অজর, অমর, অক্ষয় ও অব্যয়; কৈলাস ও তদনরূপ। ভাষাতে শব্দ নাই , বাক্যের বর্ণনা শক্তি নাই, সুতরাং কৈলাসের বর্ণনা হইল না।’ কেমন সহজ পরাভব স্বীকার, পারলাম না। পারতে চাইও না। আমি না পারলেও কিছু এসে যায় না। এ এক ধরনের নতিস্বীকার। বিরাটের কাছে এসে নিজের ক্ষুদ্রতাকে অনুভব করতে শেখা। ভ্রমণ বা তীর্থ ভ্রমণ আমাদের এই সত্যটাকে মানতে শেখায়।
কোন্ স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষের এই যাত্রা শুরু হয়েছিল চেনা পরিসর থেকে অজানার উদ্দেশ্যে, কখনও খাদ্যের প্রয়োজনে, কখনও কোনো নদীর উৎসমুখ আবিষ্কারে, কখনও নতুন ভূখেণ্ডর সন্ধানে, কখনও বা অপার্থিবের টানে। কখনও দলবদ্ধ হয়ে, কখনও একলা। দলবদ্ধ যাত্রা যখন একলার হয়ে যায় তখনই কি তা প্রকৃত ‘তীর্থ যাত্রা’ হয়ে ওঠে? জানিনা – মহাকালের রথের চাকার ঘূর্ণন যেমন সৃষ্টির আদিকাল থেকে অব্যাহত মানুষের এই যাত্রাও তেমনি কোনোদিনও থেমে যাওয়ার নয়, অন্তত যতদিন সে নিজেকে খুঁজে পেতে চায়।